ভারতীয় সভ্যতার বহুধারা
নবকুমার দাস
ভারতীয় সভ্যতা মাত্র একদিনে জন্ম নেয়নি।
তার কোনও একক নির্দিষ্ট জন্মক্ষণ নেই, নেই কোনও একক পিতৃ-মাতৃ বংশ পরিচয়। এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে ধীরে , সঞ্চিত মাটির মতো, প্রবাহিত নদীর মতো, মানুষের চলমান স্মৃতির মতো।
সে কখনও উথালপাতাল, কখনও স্থির; কখনও দৃশ্যমান, কখনও নিঃশব্দ।
ভারত মানে কোনও একটি রাজ্য নয়, কোনও একটি ধর্ম নয়, এমনকি কোনও একটি ভাষাও নয়। ভারত মানে এক দীর্ঘ মানসিক ভূগোল—যেখানে নদী শুধু জল বহন করে না, বহন করে স্মৃতি, শ্রম, বিশ্বাস ও কল্পনা।
এই সভ্যতার ইতিহাস লিখতে গেলে তাই আমাদের চোখ ফেরাতে হয় নদীর দিকে। কারণ, ভারতীয় সভ্যতা মূলত নদীনির্ভর – তার জীবনধারা জলস্রোতের সঙ্গে বাঁধা।
ভারতের কন্ঠ যদি শোনা যায় – শুধু দেখা নয় – তবে প্রথম যে শব্দটি কানে আসে, তা কোনও মানুষের কণ্ঠ নয়। সে শব্দ নদীর। এই ভূখণ্ডে নদী কখনও নিছক জলধারা ছিল না। নদী ছিল পথ, স্মৃতি, আশ্রয় এবং সময়ের নীরব ভাষ্যকার। মানুষ এসেছে, বসতি গড়েছে, প্রার্থনা করেছে, যুদ্ধ করেছে, গান গেয়েছে – আর নদী সব দেখেছে, সব বহন করেছে। বহতা নদী লিখেছে সভ্যতার কাহিনী ,সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কার্যক্রম।
ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস আসলে নদীর দীর্ঘ স্বগতোক্তি। সিন্ধু যখন ইঁটের নগরে মানুষকে আশ্রয় দিল, সরস্বতী যখন যজ্ঞের মন্ত্রে সাড়া দিল,গঙ্গা যখন প্রশ্ন করতে শেখাল তখন এই সভ্যতা নিজের পথ খুঁজে নিচ্ছিল। আর দক্ষিণে কাবেরী, কৃষ্ণা ও গোদাবরী শিল্পকে দিল শরীর; পূর্বে মহানদী দিল মানবিকতার শিক্ষা; ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা শিখিয়ে দিল প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের ভাষা; কপোতাক্ষ, কর্ণফুলি ও ইরাবতী বহন করল সীমান্ত পেরোনো স্মৃতি। এই নদীগুলি কখনও একসঙ্গে বয়ে যায়নি , কখনও এক ভাষায় কথা বলেনি। তবু তাদের স্রোত মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক সভ্যতা—যার নাম ভারতের সভ্যতা , ভারতের সংস্কৃতি ।
এই লেখাটি সেই নদীগুলির কাছে কান পেতে শোনার চেষ্টা। এ কোনও একক ইতিহাসের বিবরণ নয়; এ এক বহুস্বরে গাওয়া দীর্ঘ গান। যেখানে নগরের ইট, মন্ত্রের ধ্বনি, লোকগানের সুর আর মানুষের নিঃশ্বাস একসঙ্গে মিশে যায়। কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতি কেবল অতীতের ধ্বংসাবশেষ নয় তা আজও বয়ে চলেছে, নদীর মতো, আমাদের ভেতর দিয়ে।
ইতিহাসের এক প্রাচীন প্রভাতে, যখন মানবসভ্যতার অধিকাংশ অধ্যায় এখনও অরণ্য, গোষ্ঠী ও যাযাবরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তখন সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল এক বিস্ময়কর নগরজগত। এই নগরগুলি উচ্চস্বরে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করেনি। তারা রাজকীয় নয়, আড়ম্বরপ্রবণ নয়—তবু তাদের ভিতরে ছিল এক গভীর আত্মবিশ্বাস, এক সুসংহত যুক্তিবোধ।
হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো, ধোলাভিরা, লোথাল ইত্যাদি নামগুলি আজ আমাদের কাছে প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষা হলেও, এক সময় তারা ছিল জীবন্ত শহর। সেখানে মানুষ জেগে উঠত সকালের আলোয়, জল তুলত কুয়ো থেকে, চলত সোজা রাস্তায়, বাস করত সমান মাপের ইটের ঘরে। এই নগরজীবনে না ছিল বিশাল প্রাসাদ বা একচ্ছত্র ক্ষমতার চিহ্ন—কিন্তু ছিল পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক বোধ।
সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা আজও আধুনিক মননকে বিস্মিত করে। সমকোণী রাস্তাঘাট, পৃথক আবাসিক ও কর্মক্ষেত্র, উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা – এ সবই এক উচ্চস্তরের প্রশাসনিক ও প্রকৌশল জ্ঞানের প্রমাণ। মহেঞ্জোদড়োর নিকাশি নালা যেমন আজও কার্যকর বলে মনে হয়, তেমনই ধোলাভিরার জলসংরক্ষণ ব্যবস্থা মরুপ্রায় অঞ্চলে মানবিক অভিযোজনের এক অনন্য উদাহরণ।
এই সভ্যতার আরেকটি আশ্চর্য দিক – এর অভিন্নতা। হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চলে একই ধরনের ইট, একই ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি, একই রকম সিলমোহর—এ সবই এক বিস্তৃত সাংস্কৃতিক ঐক্যের ইঙ্গিত। তবু এই ঐক্য কোনও সাম্রাজ্যবাদী বলপ্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ যেন স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা – এক সামাজিক চুক্তি, যা নীরবে কার্যকর ছিল।
এই নীরব সভ্যতার পুনরাবিষ্কারে যে মানুষটি প্রথম ইতিহাসের মঞ্চে আলো ফেলেন, তিনি বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২২ সালে মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে এ শুধু কোনও পুরনো বসতি মাত্র নয়, এ অতি অবশ্য অনন্য এক পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার চিহ্ন। তার এই আবিষ্কার ভারতীয় ইতিহাসচর্চাকে আমূল বদলে দেয়। ভারত আর কেবল বৈদিক বা পৌরাণিক স্মৃতিতে আবদ্ধ থাকল না; তার ইতিহাস আরও গভীরে, আরও প্রাচীন কালে প্রসারিত হলো।
তবে সিন্ধু–সরস্বতী সভ্যতার ধর্মবিশ্বাস আজও রহস্যময়। কোনও বিশাল মন্দির নেই, কোনও দেবমূর্তি সর্বত্র উপস্থিত নয়। তবু সিলমোহরে পাওয়া পশুপতি সদৃশ প্রতীক, মাতৃদেবীর মূর্তি, বৃক্ষ ও প্রাণীকেন্দ্রিক চিহ্ন আমাদের ইঙ্গিত দেয়—এই সমাজ প্রকৃতি ও জীবনের পুনরুৎপাদনকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তবে মানুষের প্রতি সম্মান ছিল সবার আগে। এখানে ধর্ম ছিল সম্ভবত দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা—প্রদর্শনের নয়, অভ্যাসের বিষয়। অর্থাৎ আগে মানুষ ,মানুষের ভাবনায় হয়ত পরবর্তীতে আসে ধর্মের ভাবনা। সিন্ধু সরস্বতী সভ্যতায় রয়েছে সেই লিপি—সংক্ষিপ্ত, চিত্রধর্মী, অথচ অর্থে গভীর যা এখনো পূর্ণাঙ্গ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি । এই লিপি আজও আমাদের কাছে নীরব কোড ।
কিন্তু এই নীরবতা যেন কোনও শূন্যতা নয়; বরং এক গভীর সভ্যতাগত সংযমের চিহ্ন স্বরূপ । সব কথা লিখে রাখতে হবে এমন তাগিদ হয়ত এই সভ্যতার ছিল না।
সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার মানুষ অস্ত্র নির্মাণ জানত, কিন্তু তারা যুদ্ধপ্রবণ ছিল না। তারা বাণিজ্য করত – স্থল ও সমুদ্রপথে; তারা জিনিসপত্র মাপত, ওজন করত, হিসাবও রাখত। লোথালের বন্দরের নিদর্শন প্রমাণ করে – এই সভ্যতা সমুদ্রকে ভয় পায়নি; বরং তাকে পথ হিসেবে ব্যবহার করেছে। এছাড়া এই সভ্যতার অবসানও নাটকীয় নয়। কোনও হঠাৎ সংঘটিত ধ্বংস, কোনও সর্বগ্রাসী যুদ্ধের চিহ্ন নেই। বরং জলবায়ু পরিবর্তন, নদীপথের সরে যাওয়া, পরিবেশগত রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এই নগরগুলি ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে যায় বলেই গবেষকদের মত। আমার মনে হয় সভ্যতা হারিয়ে যায় না সে রূপ বদলায়। এই রূপান্তরের স্মৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে আজও প্রবহমান। শৃঙ্খলার প্রতি আকর্ষণ, নগর ও গ্রামের সহাবস্থান, প্রকৃতির সঙ্গে সমঝোতা এই সবের শিকড় খুঁজলে আমাদের ফিরতে হয় সেই নীরব নগরগুলির কাছে। সিন্ধু–সরস্বতী সভ্যতা তাই কেবল অতীতের অধ্যায় নয়। এটা ভারতীয় সভ্যতার প্রথম স্বর , নিম্নস্বরে উচ্চারিত, কিন্তু গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।
কিছু সভ্যতা নিজের কথা নিজে বলে। আর কিছু সভ্যতা নীরব থেকেও অন্যের স্মৃতিতে গভীর ছাপ রেখে যায়। সিন্ধু–সরস্বতী সভ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণির।
তার লিপি আজও আমাদের কাছে রহস্যময়, তার কণ্ঠস্বর নিঃশব্দ কিন্তু দূরদেশের পোড়ামাটির ফলকে খোদিত একটি নাম তাকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। সেই নামটি – মেলুহা।
মেলুহা কোনও কাব্যিক কল্পনা নয়, কোনও পুরাণের দেশও নয়। এই নাম উঠে এসেছে মেসোপটেমিয়ার প্রশাসনিক নথি, রাজকীয় শিলালিপি ও বাণিজ্যসংক্রান্ত দলিল থেকে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে সুমের ও আক্কাদের রাজারা যখন নিজেদের সাম্রাজ্যের বিস্তার লিপিবদ্ধ করছেন, তখনই তারা উল্লেখ করছেন এক দূরবর্তী ভূখণ্ডের-সমুদ্র পেরিয়ে যার সঙ্গে যোগাযোগ,যার পণ্য দুর্লভ, যার মানুষ কথা বলে আলাদা ভাষায়।
এই দূরত্বের মধ্যেই মেলুহার পরিচয়। মেসোপটেমীয় লেখায় মেলুহা কখনও ‘বিস্ময়ের দেশ’, কখনও ‘সম্পদের ভাণ্ডার’। সেখানে পৌঁছতে হয় জলপথে; সেখানকার মানুষ কথা বলে এমন এক ভাষায়, যার জন্য প্রয়োজন হয় দোভাষীর। একটি বিশেষ শব্দ আমাদের আবিষ্ট করে রাখে , “মেলুহান দোভাষী” এই প্রেক্ষিতে গভীর তাৎপর্য বহন করে। কারণ, দোভাষীর উপস্থিতি মানেই কেবল যোগাযোগ নয় নিয়মিত, সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ।
তাহলে মেলুহা থেকে কী আসত ?
মেসোপটেমীয় নথি জানায় যে মেলুহা থেকে আসে কর্ণেলিয়ান পুঁতি, ল্যাপিস লাজুলি, মূল্যবান কাঠ, হাতির দাঁত, সম্ভবত তুলো ও সূক্ষ্ম বস্ত্র।
আজকের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দেখায় যে এই কর্নেলিয়ান পুঁতির উৎস গুজরাট ও সিন্ধু অঞ্চলে; লোথাল ও ধোলাভিরার মতো বন্দরের নিদর্শন এই বাণিজ্যের বাস্তব ভিত্তি। অর্থাৎ, মেলুহা কোনও বিমূর্ত ধারণা নয়—সে ছিল এক বাস্তব ভূখণ্ড, বাস্তব সমাজ, বাস্তব অর্থনৈতিক শক্তি। এইখানেই সিন্ধু–সরস্বতী সভ্যতার এক গভীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তারা কেবল নগর গড়েনি, কেবল পরিকল্পনা করেনি – তারা বিশ্বে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছিল। তারা জানত ওজনের মান, পরিমাপের শৃঙ্খলা, চুক্তির মূল্য। তারা সমুদ্রকে অতিক্রম করেছিল, অথচ তাকে দখল করেনি।
অর্থাৎ মেলুহা ছিল সিন্ধু সভ্যতার বহির্বিশ্বে প্রতিফলিত মুখ যেখানে তার নিজস্ব লিপির নীরবতা ভেঙে কথা বলে অন্যের কলম।
আরও এক আশ্চর্য মিল লক্ষণীয়।
খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৯০০ অব্দ নাগাদ, যখন সিন্ধু নগরগুলির সংগঠিত নগরজীবন ধীরে ধীরে রূপ বদলাতে শুরু করে ঠিক তখনই মেসোপটেমীয় নথি থেকে মেলুহার নাম হারিয়ে যেতে থাকে। ইতিহাসে এই সমকালীন নীরবতা কাকতালীয় নয়। এ যেন এক সভ্যতার আন্তর্জাতিক পরিচয়ের সূর্যাস্ত।
কিছু গবেষক লক্ষ করেছেন যে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত ম্লেচ্ছ শব্দটির সঙ্গে মেলুহা-র ধ্বনিগত সাযুজ্য। এই মিল নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পথ না দেখালেও, একটি সাংস্কৃতিক স্মৃতির ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত দেয়। নাম বদলায়, ভূগোল বদলায় কিন্তু স্মৃতির ছায়া রয়ে যায়।
মেলুহা আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে করিয়ে দেয় যে ভারতীয় সভ্যতা কখনও প্রান্তিক ছিল না। সে নিজেকে বিশ্ব থেকে দূরে সড়িয়ে রাখেনি, আবার বিশ্বকেও নিজের উপর চাপিয়ে দিয়ে ভারাক্রান্ত করেনি ।
তার সম্পর্ক ছিল আদান-প্রদানের, শোষণের নয়। শাসনের নয়। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মানপ্রদর্শনই যেন তার মহাব্রত।
এই অর্থে মেলুহা হল সিন্ধু–সরস্বতী সভ্যতার প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়।এ এমন এক সভ্যতা, যা নিজের কথা নিজে লিখে যায়নি কিন্তু এমন ছাপ রেখে গেছে, যা অন্য সভ্যতাকে লিখতে বাধ্য করেছে। আজ, যখন আমরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে কেবল আধ্যাত্মিকতা বা অন্তর্মুখিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখতে চাই, তখন মেলুহার স্মৃতি আমাদের সতর্ক করে। এই সংস্কৃতির শিকড় যেমন গভীর, তেমনই তার দৃষ্টি ছিল দূরপ্রসারী। মেলুহা তাই কোনও হারিয়ে যাওয়া নাম নয়। সে হল আয়নার মতো যেখানে অপরের চোখে আমরা প্রথমবার নিজেদের দেখি। আবিষ্কার করি নিজেদেরই।
এই পর্বে ভারতীয় সভ্যতা শিখে নেয় এক অনন্য শিক্ষা, একাধিক সত্য পাশাপাশি বাঁচতে পারে।
সভ্যতার ইতিহাস কেবল স্থলভাগের ইতিহাস নয়। মানুষ যেমন নদীর তীরে বসতি গড়েছে, তেমনই সমুদ্রকে করেছে পথ। এই পথ ধরেই ভারতীয় উপমহাদেশ তার প্রথম বিশ্ব-পরিচয় পেয়েছিল। সিন্ধু–সরস্বতী সভ্যতার আন্তর্জাতিক রূপ বুঝতে গেলে আমাদের চোখ ফেরাতে হয় আরব সাগরের দিকে কারন সেখানে এক প্রাচীন সমুদ্রপথ আজও ইতিহাসের মানচিত্রে নীরবে আঁকা আছে। এই পথের তিনটি প্রধান বিন্দু যথাক্রমে , মেলুহা, লোথাল ও ওমান।
আগেই বলেছি যে মেসোপটেমীয় নথিতে উল্লিখিত মেলুহা নামটি আজ গবেষকদের কাছে পরিচিত সিন্ধু–সরস্বতী সভ্যতার বহির্বিশ্বে ব্যবহৃত পরিচয় হিসেবে। মানচিত্রে এই অঞ্চল বর্তমান সিন্ধু নদী অববাহিকা ও গুজরাট উপকূলকে ঘিরে বিস্তৃত। এই ভূখণ্ড ছিল উৎপাদনের কেন্দ্র। এখানে তৈরি হতো কর্নেলিয়ান পুঁতি, সূক্ষ্ম কারুশিল্প, তুলো ও কাঠের দ্রব্য। নদীপথে এই পণ্যগুলি পৌঁছত উপকূলের দিকে যেখানে স্থলভাগ সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অর্থাৎ মেলুহা ছিল এমন এক সভ্যতা, যে নিজের ভেতরে সংগঠিত, কিন্তু চোখ রেখেছিল সুদূর দিগন্তে। গুজরাট উপকূলে অবস্থিত লোথাল ছিল সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগর। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া বৃহৎ জলাধারকে বহু গবেষক বিশ্বের প্রাচীনতম ডকইয়ার্ড বলে মনে করেন। লোথাল ছিল সেই জায়গা, যেখানে স্থলভাগের উৎপাদিত পণ্য প্রথমবার সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি নিত। নদীপথে আসা সামগ্রী এখানে মজুত হতো, যাচাই হতো ওজন ও মাপে, তারপর জাহাজে তোলা হতো।অর্থাৎ মানচিত্রে লোথাল ছিল এক কৌশলগত বিন্দু যেখান থেকে আরব সাগরের জলপথ সরাসরি পশ্চিমে ওমান ও আরও দূরে মেসোপটেমিয়ার দিকে নিয়ে যেত।যেমনটা ঘটে বর্তমান মুম্বাই ও কান্দালা বন্দরে। লোথাল তাই কেবল একটি বন্দর নয় সে ছিল সভ্যতার দরজা। বাণিজ্যের সূচনা। আরব সাগর পেরিয়ে পশ্চিমে তাকালে দেখা যায় ওমান উপদ্বীপ। প্রাচীন মেসোপটেমীয় লেখায় এই অঞ্চল পরিচিত ছিল মাগান নামে। ওমান ছিল এই বাণিজ্যপথের মধ্যবর্তী স্তম্ভ। এখানে পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতার ধাঁচের সিলমোহর, কর্নেলিয়ান পুঁতি ও তামা খনির নিদর্শন। এই প্রমাণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ওমান কেবল গন্তব্য নয়, বরং এক ট্রানজিট জোন। যেন বর্তমানের দুবাই কিংবা ইস্তাম্বুল।এখানে এসে জাহাজগুলো বিশ্রাম নিত, পণ্য বিনিময় হতো, আবার নতুন যাত্রার প্রস্তুতি নিত। এই অঞ্চলের তামা সিন্ধু সভ্যতার ধাতুশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।
এই বাণিজ্যপথ কোনও কাকতালীয় যাত্রার ফল নয়। এটি ছিল নিয়মিত, মৌসুমি ও পরিকল্পিত। তাহলে সিন্ধু সভ্যতার নাবিকরা জানত মৌসুমি বায়ুর দিক, সমুদ্রের স্রোত ও নক্ষত্রের দিক নির্দেশ। এই জ্ঞান ছাড়া আরব সাগর অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ, এই সভ্যতা কেবল নগর নির্মাণে নয় নৌপ্রযুক্তিতেও দক্ষ ছিল।
এই সমুদ্রপথের শেষ প্রান্তে ছিল মেসোপটেমীয় নগর উর, উরুক, লাগাশ ইত্যাদি। এখানেই মেলুহার নাম উঠে আসে রাজকীয় নথিতে। মেসোপটেমীয় লেখায় উল্লেখিত “মেলুহান দোভাষী” প্রমাণ করে এই সম্পর্ক ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক। এখানে মেলুহা কোনও অচেনা দেশ ছিলনা ; বরং তা ছিল পরিচিত বাণিজ্যিক অংশীদার। এই মেলুহা–লোথাল–ওমান বাণিজ্যপথ আমাদের একটি মৌলিক সত্য শেখায়। শেখায় সিন্ধু–সরস্বতী সভ্যতা প্রাচীন বিশ্বের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও বিচ্ছিন্ন সমাজ ছিল না। সে ছিল সংযুক্ত, সচেতন ও বিশ্বমুখী। এখনকার ভাষায় ট্রেন্ডি। এই পথ ধরে কেবল পণ্য নয় ধারণা, নান্দনিকতা ও সভ্যতার স্মৃতি আদান-প্রদান অবশ্যই হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার প্রথম বিশ্বযাত্রা শুরু হয়েছিল এই সমুদ্রপথেই , নীরবে, পরিকল্পিতভাবে, কিন্তু গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে।
অন্যদিকে দেশের ভিতরে দীর্ঘতম জলধারার নাম গঙ্গা নদী। তবে গঙ্গা কেবল জলধারা নয়। গঙ্গা একটি দীর্ঘ চিন্তার স্রোত যেখানে জল বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বয়ে চলে মানুষের বিশ্বাস, দর্শন ও স্মৃতি। এই নদীর জন্ম যেমন হিমালয়ের বরফে, তেমনই তার প্রকৃত উত্স মানবচেতনায়। মানচিত্রে গঙ্গা শুরু হয় গোমুখে। কিন্তু সভ্যতার মানচিত্রে তার উত্স আরও গভীরে যেখানে মানুষ প্রথম উপলব্ধি করেছিল, প্রকৃতি কেবল বেঁচে থাকার সহায় নয়, ভাবনার আধার।
সিন্ধু–সরস্বতী সভ্যতার নগরভিত্তিক সংগঠন ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর, উত্তর ভারতের সমতলে গঙ্গা এক নতুন সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই উপত্যকায় আর নগর প্রথমে প্রধান নয় , প্রধান হয়ে ওঠে কৃষি, গ্রাম ও দীর্ঘস্থায়ী বসতি। গঙ্গার বার্ষিক প্লাবন জমিকে উর্বর করেছিল, মানুষকে শিখিয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাত নয়, সহাবস্থান।
এখানেই জন্ম নেয় জনপদ—কৌশাম্বী, বারাণসী, পাটলিপুত্র। এখন নগরগুলি আর কেবল প্রশাসনিক নয়,তারা হয়ে ওঠে বুদ্ধিবৃত্তির কেন্দ্র।
তবে ঋগ্বেদে গঙ্গার উল্লেখ আছে সামান্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে গঙ্গা হয়ে ওঠে চিন্তার প্রতীক। এই উপত্যকাতেই মানুষ প্রশ্ন করতে শেখে, সে কে ? আত্মা কী ? ব্রহ্ম কী ? জীবনের পরিণতি কোথায় ? ইত্যাদি ইত্যাদি। গঙ্গার প্রবাহ যেন এই প্রশ্নগুলির ভাষা।
তার ধারাবাহিকতা মানুষকে শিখিয়েছে – সবকিছু বদলায়, তবু ধারাটি থাকে। উপনিষদের নেতি নেতি দর্শন যেন গঙ্গার জল- ধরা যায় না, অথচ অস্বীকারও করা যায় না। গঙ্গা উপত্যকাতেই জন্ম নেয় বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তা। লুম্বিনী, বোধগয়া, সারনাথ – এই সব স্থান একে অপরের সঙ্গে যুক্ত নদীপথে। এখানে গঙ্গা কেবল পবিত্র নয়- সে যেন কালের সাক্ষী। বুদ্ধের মধ্যম পথ, মহাবীরের অহিংসা- এই দর্শনগুলি নদীর মতোই প্রবাহমান, কোনও একক কেন্দ্রে আবদ্ধ নয়। গঙ্গা এখানে ধর্মের জল নয় – নৈতিকতার প্রবাহ।
মৌর্য যুগে গঙ্গা উপত্যকা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র। পাটলিপুত্রের অবস্থান কোনও দৈব ঘটনা নয় বরং এটি ছিল নদীপথ নিয়ন্ত্রণের কৌশলগত অবস্থান । অর্থশাস্ত্রে গঙ্গা উপত্যকার কৃষি, নৌপথ ও বাণিজ্যের বিশ্লেষণ একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এখানে গঙ্গা রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড- যে জল সরবরাহ করে খাদ্য, যোগাযোগ ও কর ব্যবস্থা।
গঙ্গা ভারতীয় সংস্কৃতিকে দিয়েছে দৈনন্দিন ছন্দ। সকাল শুরু হয় গঙ্গাস্নানে,শেষ হয় তার তীরে দাহকর্মে । জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু – জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব গঙ্গাকে সাক্ষী রেখেই সংঘটিত হয় যেন। সবকিছুতেই গঙ্গা উপস্থিত। এখানে নদী দেবী হলেও, সে দূরের অলৌকিক শক্তি নয় , সে যেন ঘরের সদস্য। মহাভারতে গঙ্গা দেবী হয়ে ওঠেন রাজবধূ।
তবে গঙ্গা আমাদের শিখিয়েছে এক মৌলিক সত্য – সভ্যতা কোনও স্থির স্থাপত্য নয়, সে এক চিরন্তন প্রবাহ। এই নদীর তীরে মানুষ শিখেছে স্মরণ করতে, ভুলে যেতে, আবার নতুন করে শুরু করতে। গঙ্গা তাই শুধুমাত্র নদী নয় সে এক প্রশ্নবহুল পথ। যেখানে জল বয়ে যায় সামনে,কিন্তু দৃষ্টি ফেরে অন্তরে।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু–সরস্বতীর নগরগুলি স্তব্ধ হয়। সভ্যতার কেন্দ্র সরে আসে পূর্ব দিকে—গঙ্গা–যমুনা উপত্যকায়। এখানে সভ্যতার ভাষা বদলে যায়। ইট ও নিকাশির জায়গায় আসে প্রশ্ন: আমি কে? জীবন কী? মুক্তি কী?
বৈদিক স্তোত্র, উপনিষদের সংশয়, বুদ্ধের করুণা, মহাবীরের সংযম ইত্যাদি সবই এই নদীর তীরে জন্ম নেয়। গঙ্গা এখানে কেবল কৃষির সহায় নয়; সে হয়ে ওঠে চিন্তার ধারক। এই পর্বে ভারতীয় সভ্যতা শিখে নেয় এক অনন্য শিক্ষা—একাধিক সত্য পাশাপাশি বাঁচতে পারে।
গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতা ছিল শিল্পমুখর। এখানে দেবতা পাথরে কথা বলেন, সংগীতে নেমে আসেন, নৃত্যে শরীর ধারণ করেন। চোল মন্দিরের প্রাচীর, সঙ্গম সাহিত্যের পংক্তি, ভক্তি আন্দোলনের গান সব মিলিয়ে দক্ষিণ ভারত ভারতীয় সংস্কৃতিকে দেয় তার নান্দনিক গভীরতা। এখানে সংস্কৃতি ছিল শাস্ত্রনির্ভর, কিন্তু জীবনের সঙ্গে যুক্ত।
মহানদী উপত্যকায় কলিঙ্গ সভ্যতা মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার তীরে সভ্যতা শেখে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান। আর বাংলা তো নদীর দেশ। কপোতাক্ষ, ভাগীরথী, পদ্মা যমুনা এই নদীগুলি কেবল জল নয়, ভাষা, সাহিত্য ও অনুভবের আধার। মাইকেল মধুসূদনের কপোতাক্ষ হোক বা লোকগানের নদীস্মৃতি বাংলার সংস্কৃতি নদীর সঙ্গেই কথা বলে।
সমকালীন লেখক অমিশ ত্রিপাঠি বলেছেন—ভারত ভাঙে না, সে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের প্রকৃত নকশা আঁকে তার নদীগুলি। কখনও তারা শুকিয়ে যায়, কখনও পথ বদলায় কিন্তু সভ্যতার স্রোত থামে না।
এই ধারাবাহিক প্রবন্ধ মালার সূচনায় এই লেখার উদ্দেশ্য একটাই ভারতীয় সভ্যতাকে কোনও একক সূত্রে বেঁধে না ফেলে, তার বহুস্বর, বহুধারা ও বহুরূপকে চিনে নেওয়া। কারণ, ভারতের সংস্কৃতি কোনও অতীত নয় সে আজও প্রবাহমান, ঠিক নদীর মতো।

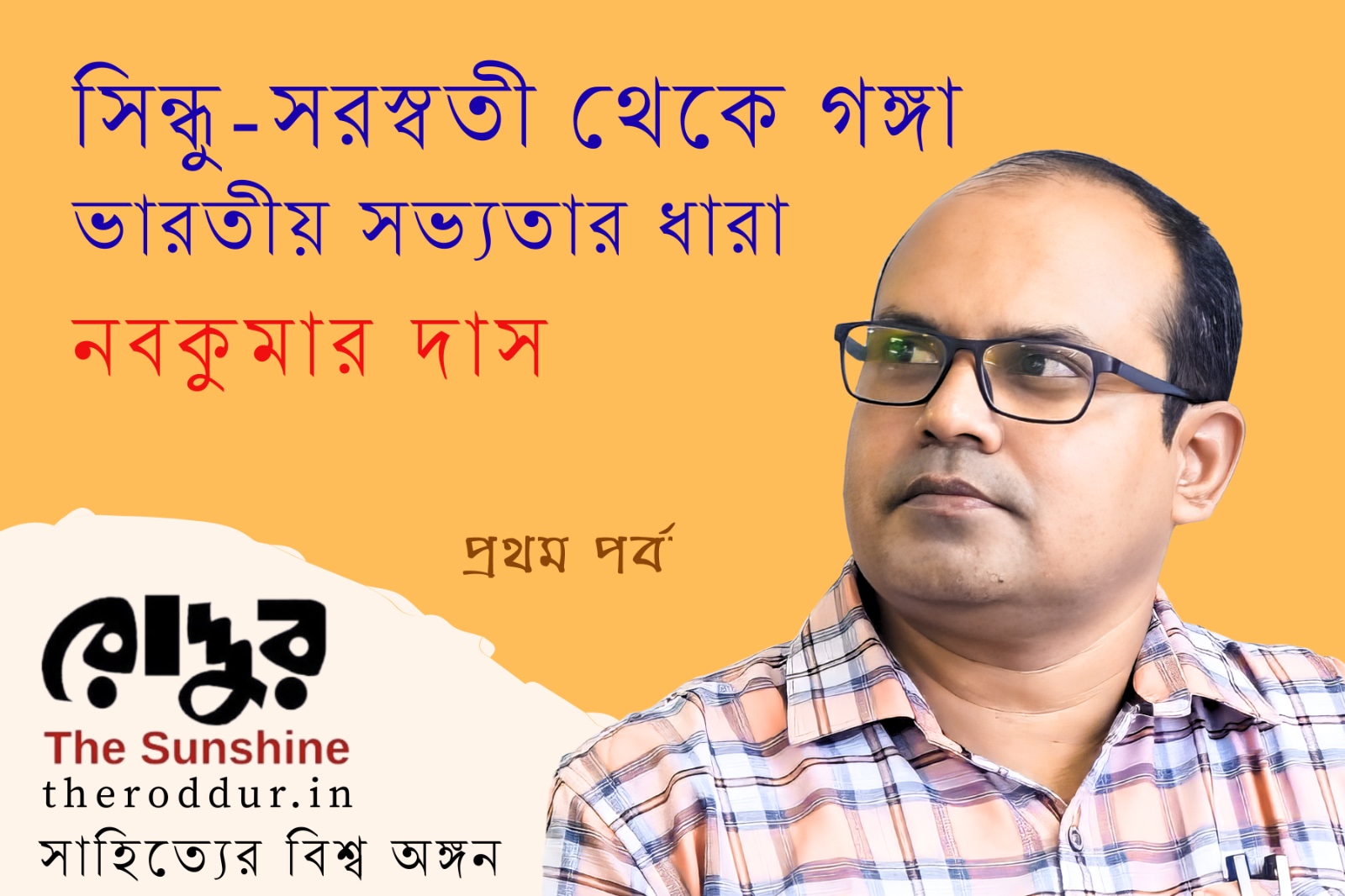





2 Responses
Very well described
খুব ভালো লাগল। পরের পর্বের অপেক্ষায় রইলাম।
শুভাশিস ঘোষ