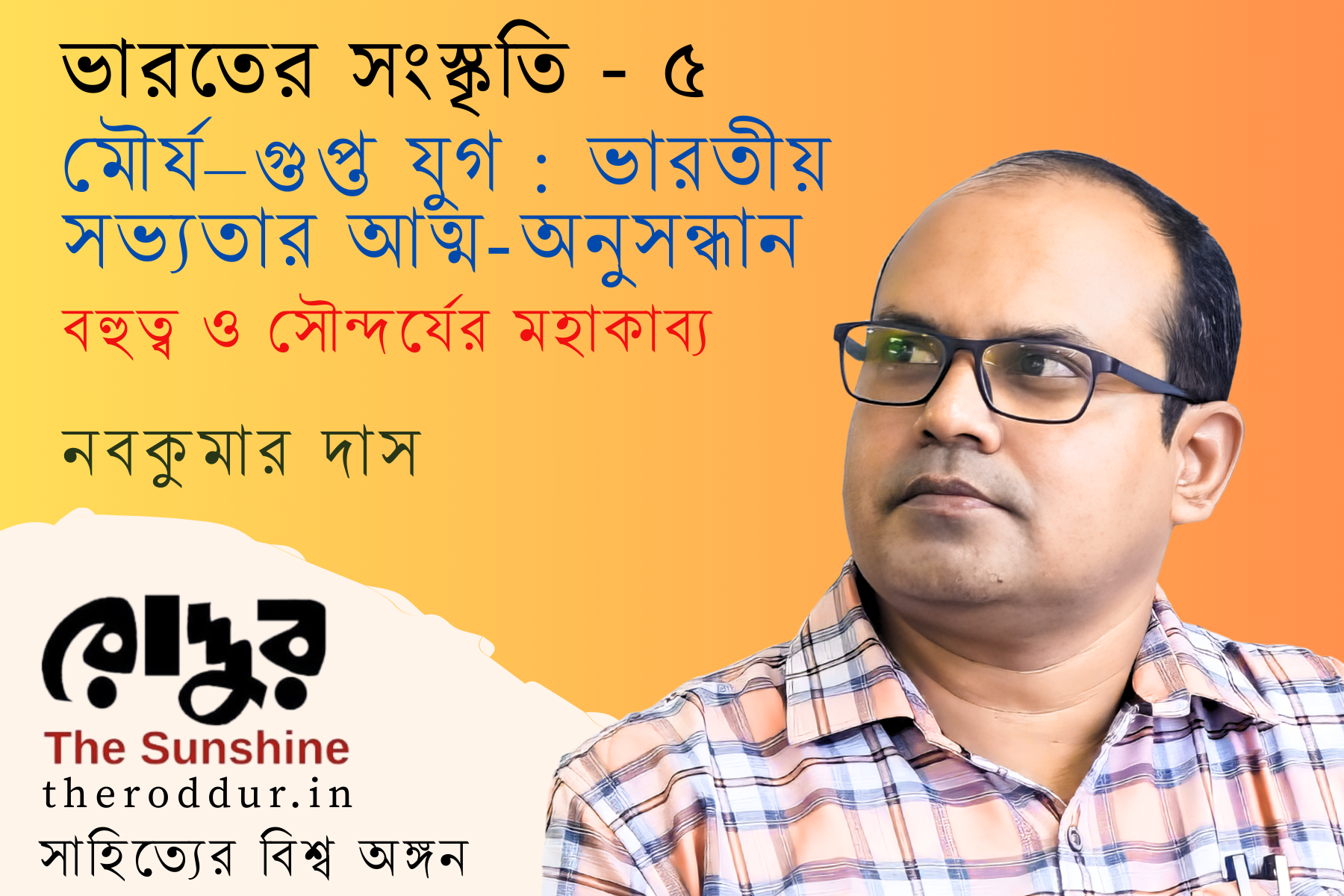বহুত্ব ও সৌন্দর্যের মহাকাব্য
নবকুমার দাস
বৈদিক সূর্যাস্ত আর মৌর্য সূর্যোদয়ের মাঝখানে যে দীর্ঘ গোধূলিক্ষণ, সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে ভারতের ইতিহাসের এক গভীর, বহুমাত্রিক অধ্যায়। এ যুগ কোনো একক সাম্রাজ্যের নামে চিহ্নিত নয়, তবু এই সময়েই ভারতের আত্মা ধীরে ধীরে নিজের রূপ খুঁজে পায়। এ যেন এক দীর্ঘ শ্বাস – যেখানে পুরনো মন্ত্রের ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে আসছে , আর নতুন চিন্তার পদচিহ্ন আঁকা হবে শ্বাশত ভারতের পথে-প্রান্তরে ।
বৈদিক যুগের শেষপ্রান্তে মানুষ তখন আর শুধু যজ্ঞবেদির চারপাশে আবদ্ধ নয়। ঘণ্টাধ্বনি আর অরণ্যের স্তব্ধতার মাঝখানে উঠে আসছে গ্রামীন ভারতের কলরব, চলিষ্ণু জনপদের অনন্ত গুঞ্জন,
নদীতীরে গড়ে উঠছে নতুন বসতি – গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নতুন সমাজের স্বপ্ন। অরণ্য আশ্রমের ধ্যানী ঋষির পাশে দাঁড়িয়ে পড়ছে কৃষক, কারিগর, ব্যবসায়ী। জীবন আর শুধু দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ নয়- জীবন হয়ে উঠছে মানুষের নিজের জন্যও।
এই সময়ে যজ্ঞ চলছে, কিন্তু যজ্ঞের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে প্রশ্ন। কে আমি ? এই জগতের শুরু কোথায় ? দেবতারা কি সত্যিই সর্বশক্তিমান, নাকি তাদেরও ওপরে আছে কোনো অদৃশ্য সত্য? – এই প্রশ্নগুলোই ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে উপনিষদের ভাষায় – নিস্তব্ধ, গভীর, নির্ভীক। ব্রহ্ম আর আত্মা এক – এই উচ্চারণ যেন বজ্রের মতো গম্ভীর তা যেন ভেঙে দেয় বহিরঙ্গ আচারকেন্দ্রিক ধর্মের দেয়াল।
এই গোধূলি যুগেই আবির্ভূত হন গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর আরও অসংখ্য ভ্রাম্যমাণ সাধক। তারা বললেন – মুক্তি যজ্ঞে নয়, মুক্তি করুণায়, মুক্তি সংযমে, মুক্তি অন্তর্দৃষ্টিতে। বনের পথ ধরে হাঁটা সন্ন্যাসীর পায়ের শব্দ নতুন ভারতের মানচিত্র আঁকতে থাকে। তারা গ্রাম ছেড়ে আসছে নগরে। রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, তক্ষশীলা – সে এক দীর্ঘ তালিকা। এই নামগুলো তখন কেবল স্থান নয়, সভ্যতার নবজাত কেন্দ্র। এগুলোর বাজারে বন্দরে শোনা যাচ্ছে নানা ভাষা, মুদ্রার ঝংকারে বদলে যাচ্ছে বিনিময়ের রীতি। কারিগরের হাতে জন্ম নিচ্ছে লোহার অস্ত্র, মাটির পাত্র, সূক্ষ্ম অলংকার ইত্যাদি। সমাজে জন্ম নিচ্ছে নতুন শ্রেণি – শ্রেষ্ঠী, গৃহপতি, বণিক। জাতকের গল্পে যে তার ছায়া ছায়া নির্মাণ দেখি আমরা। জীবন ধীরে ধীরে ধর্মীয় আচার থেকে অর্থনৈতিক বাস্তবতার দিকে ঝুঁকছে।
ঠিক এইসময় ষোড়শ মহাজনপদগুলোর উত্থান ঘটেছিল। মূলত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে (৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। আর গুপ্ত যুগ শুরু হয়েছিল তার প্রায় ৮০০-৯০০ বছর পর (৩২০ খ্রিষ্টাব্দ)। অর্থাৎ, মহাজনপদগুলো বুদ্ধদেবের সময়ের সমসাময়িক। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ‘অঙ্গুত্তর নিকায়’ অনুযায়ী ১৬টি মহাজনপদের নাম পাওয়া যায়। তবে, পরবর্তীতে চারটি রাজ্য বাকিদের হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যেমন , মগধ (Magadha) ছিল বর্তমান দক্ষিণ বিহারের অংশ । এর রাজধানী ছিল রাজগৃহ (গিরিব্রজ) এবং পরে পাটলিপুত্র। এই মগধ-ই শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান অযোধ্যা ও উত্তরপ্রদেশ অঞ্চল জুড়ে বিস্তারিত কোশল (Kosala) এর রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ও বিখ্যাত শাসক ছিলেন। তৃতীয়তঃ বর্তমান মালব বা মধ্যপ্রদেশ অঞ্চল জুড়ে ছিল অবন্তী (Avanti)। এর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। রাজা প্রদ্যোত ছিলেন এখানকার প্রভাবশালী শাসক। এছাড়া , বর্তমান এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ) অঞ্চল ছিল বৎস (Vatsa) রাজ্যের অন্তর্গত । রাজধানী ছিল কৌশাম্বী। রাজা উদয়ন ছিলেন এখানকার জনপ্রিয় শাসক। মনে রাখতে হবে এখন রাজা আর শুধু যোদ্ধা নন, তিনি একই সঙ্গে প্রশাসক। কর আদায়, সেনাবাহিনী, আইন প্রণয়ন ও পালন ইত্যাদি তার দৈনিন্দিন কর্তব্যে পরিণত হল। রাষ্ট্র ধীরে ধীরে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠছে। এ যেন মৌর্য সাম্রাজ্যের অদৃশ্য পূর্বপ্রস্তুতি। তবে এই যুগ শান্ত নয়। এ যুগে তর্ক আছে, বিতর্ক আছে, সংঘাত আছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে শ্রমণ ধারার দ্বন্দ্ব, যজ্ঞের পাশে থাকে বুদ্ধের মৌনতা। তবু এই দ্বন্দ্ব ধ্বংস নয়, এই দ্বন্দ্ব সৃজন। এই সংঘাতের গর্ভেই ভারতের বৈচিত্র্য জন্ম নিচ্ছে ।
মধ্যবর্তী এই সময়ে ভারত ধীরে ধীরে দেবকেন্দ্রিকতা থেকে মানবকেন্দ্রিকতার দিকে এগোচ্ছে। মানুষের দুঃখ, মানুষের মুক্তি, মানুষের দায়িত্ব – এসবই হয়ে উঠছে চিন্তার কেন্দ্রে। বৈদিক ও মৌর্য যুগের মাঝখানের এই সময় কোনো ছায়াযুগ নয়, এ হলো বীজবপনের যুগ। এই সময়ে বোনা বীজ থেকেই মৌর্য সাম্রাজ্যের বিশাল বৃক্ষ জন্ম নেবে, আর ভারতের আত্মা পাবে তার বহুবর্ণ, বহুস্বর রূপ। এ এক দীর্ঘ গোধূলি – যেখানে দিনের আলো ফুরোচ্ছে, কিন্তু রাত নামার আগেই যেন নতুন এক সূর্যের আভাস দেখা যাচ্ছে।
এই দীর্ঘ সভ্যতার ইতিহাসে তাই মৌর্য -গুপ্ত যুগ এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ। এখানে ভারত প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক ঐক্য, দার্শনিক বহুত্ব ও সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় অর্জন করে। মৌর্য যুগ রাষ্ট্রকে দৃঢ় করে, গুপ্ত যুগ আত্মাকে সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করে। এই দুই যুগ মিলেই নির্মাণ করে ভারতীয় সভ্যতার এক গভীর পরিচয় – যেখানে ক্ষমতা ও করুণা, ধর্ম ও যুক্তি, ঐতিহ্য ও পরিবর্তন একসঙ্গে সহাবস্থান করে।
মৌর্য–গুপ্ত যুগকে বুঝতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় বৈদিক সভ্যতার দিকে। ঋগ্বেদের স্তোত্রে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক – “একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।” (ঋগ্বেদ, ১.১৬৪.৪৬) অর্থাৎ, সত্য এক, কিন্তু জ্ঞানীরা তাকে নানা নামে অভিহিত করেন। এই একটি পংক্তির মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতার মৌল দর্শন নিহিত। সত্য এক, কিন্তু তার প্রকাশ বহুবিধ। এখানেই ভারতীয় চিন্তার বহুত্বের বীজ রোপিত হয়।
উপনিষদে এই বহুত্ব আরও গভীর হয়ে ওঠে – “অহং ব্রহ্মাস্মি।” (বৃহদারণ্যক উপনিষদ) এবং “তত্ত্বমসি।” (ছান্দোগ্য উপনিষদ) অর্থাৎ এখানে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যের ধারণা ভারতীয় দর্শনের এক শিখরবিন্দু হয়ে ওঠে । মানুষের আত্মা এবং বিশ্বসত্তা আলাদা নয় – এই উপলব্ধি পরবর্তী যুগের সমস্ত ধর্ম ও দর্শনের ভিত নির্মাণ করে। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক ঐক্যের পাশাপাশি বৈদিক সমাজে ছিল কঠোর যজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মব্যবস্থা,বর্ণভিত্তিক সামাজিক কাঠামো ও পুরোহিততন্ত্র। এখান থেকেই জন্ম নেয় প্রতিসংস্কৃতি বা counter culture – শ্রমণ আন্দোলন।
বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে এক বিপ্লবী ঘটনা। তারা বৈদিক ধর্মের আচারকেন্দ্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে অস্তিত্বগত প্রশ্ন তোলে। বুদ্ধ ঘোষণা করেন – “সব্বং অনিচ্চং।”- (ধম্মপদ) অর্থাৎ জগতের সবকিছুই অনিত্য। কোনো স্থায়ী আত্মা নেই—এই ধারণা উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে এক গভীর প্রশ্ন। অন্যদিকে বুদ্ধের চার আর্যসত্য—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ—মানুষের মুক্তির এক মানবিক পথ নির্দেশ করে। এখানে মুক্তি কোনো আকাশচারী ধারণা নয়; এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত।
অন্যদিকে মহাবীরের জৈন দর্শন আত্মার চিরন্তনতা স্বীকার করে, কিন্তু তাকে বন্ধনগ্রস্ত বলে মনে করে। অহিংসা এখানে কেবল নৈতিক আদর্শ নয়; এটি অস্তিত্বের মৌলনীতি। এই দুই দর্শন ভারতীয় চিন্তাজগতে এক নতুন ভাষা এনে দেয় যেখানে প্রশ্ন করা কোনও পাপ নয়, বরং সাধনার পথ।
এই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উত্থানের মাধ্যমে ভারত প্রথমবারের মতো এক শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করে। কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ এই রাষ্ট্রব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করে। কৌটিল্য রাষ্ট্রকে দেখেছিলেন বাস্তববাদী দৃষ্টিতে। তাঁর কাছে ক্ষমতা নৈতিকতার বিপরীত নয়; বরং ক্ষমতা ও নৈতিকতার মধ্যে এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য প্রয়োজন। অর্থশাস্ত্রে তিনি লিখেছেন, “প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ।” অর্থাৎ রাজ্যের সুখ নির্ভর করে প্রজার সুখের ওপর। এই ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে বিস্ময়করভাবে সাযুজ্যপূর্ণ।
তাঁর পথ ধরেই অশোক ক্ষমতার দাম্ভিক উচ্চতা থেকে নেমে আসেন করুণার অপার জলধির দিকে। আমরা দেখি মৌর্য যুগের সবচেয়ে গভীর রূপান্তর ঘটে অশোকের হাতে। কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে উপলব্ধি করায়—জয় মানে কেবল ভূখণ্ডের দখল নয়; জয় মানে মানুষের হৃদয়ের রূপান্তর। এই রূপান্তরের ছায়া দেখি অশোকের অসংখ্য শিলালিপিতে। অশোকের শিলালিপিতে আমরা পড়ি, “সব প্রাণীর প্রতি দয়া।”
অশোকের ‘ধর্ম’ কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদ নয়; এটি এক মানবিক নৈতিকতা। এখানে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব স্পষ্ট, কিন্তু অশোক কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র নির্মাণ করেননি। তিনি নির্মাণ করেছিলেন এক নৈতিক রাষ্ট্র। এই মুহূর্তটি ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানেই প্রথমবার রাষ্ট্রনীতি ও করুণার দর্শন একত্রিত হয়।
কালের নিয়মে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষ রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়। কিন্তু এই রাজনৈতিক দুর্বলতার মধ্যেই সাংস্কৃতিক শক্তি আরও গভীর হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিকশিত হয় নানা শিল্পরীতি, ধর্মীয় সম্প্রদায় ও দর্শনধারা। শক, কুষাণ, পার্থিয়ান ইত্যাদি বিদেশি শক্তির আগমন ভারতীয় সভ্যতাকে দুর্বল করেনি; বরং তাকে আরও বহুমাত্রিক করেছে। কুষাণ যুগে গান্ধার শিল্পে গ্রিক ও ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণ ঘটে। বুদ্ধমূর্তির মানবিক রূপ এই সময়েই প্রথম স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এটি প্রমাণ করে যে ভারতীয় সভ্যতা কখনোই বন্ধ দরজা ছিল না; বরং এটি ছিল এক উন্মুক্ত সংলাপ।
এরপর আসে গুপ্ত যুগ যা প্রকৃত অর্থেই সৌন্দর্যের রাজত্ব। গুপ্ত যুগকে প্রায়ই “ভারতের স্বর্ণযুগ” বলা হয়। কিন্তু এই স্বর্ণযুগ কেবল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বা সামরিক সাফল্যের ফল নয়; এটি ছিল গভীরতর এক সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের ফল যে সময়ে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক চেতনা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ সভ্যতার রূপ নির্মাণ করেছিল। এই যুগে সৌন্দর্য আর উপযোগের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না; বরং সৌন্দর্যই ছিল সত্যের বাহন, আর শিল্প ছিল আত্মার ভাষা।
গুপ্ত শাসনকালে সমাজব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি সুসংহত ছিল, এবং বাণিজ্যপথ স্থল ও সমুদ্র – উভয় দিকেই বিস্তৃত ছিল। এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা শিল্পী ও চিন্তাবিদদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। ফলে শিল্প কেবল রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার বিষয় হয়ে থাকেনি; এটি ধীরে ধীরে সমাজের অন্তঃস্থ সৃজনশীল চেতনার অংশ হয়ে উঠেছিল।
অজন্তার গুহাচিত্রে আমরা দেখি মানুষের আবেগ, করুণা ও সৌন্দর্যের এক অনন্য প্রকাশ। এখানে বুদ্ধের জীবনকাহিনি, জাতক উপাখ্যান ও সমসাময়িক সমাজজীবনের দৃশ্যাবলি এমনভাবে অঙ্কিত হয়েছে যে, সেগুলো নিছক ধর্মীয় বর্ণনা নয়—বরং মানব অস্তিত্বের অন্তর্লীন অনুভূতির দলিল। নারীর মুখাবয়বে লাজুকতা, রাজপুরুষের দৃষ্টিতে আত্মমর্যাদা, সন্ন্যাসীর চোখে নির্লোভ শান্তি—সবকিছুই রঙ ও রেখার মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ অজন্তার শিল্পীরা জানতেন, সৌন্দর্য কেবল বাহ্যিক নয়; সৌন্দর্য নিহিত থাকে অনুভূতির সূক্ষ্ম প্রকাশে। তাই অজন্তার চিত্রকলা আমাদের সামনে এক মানবিক নন্দনতত্ত্ব তুলে ধরে, যেখানে দয়া, প্রেম, বেদনা ও আশার সম্মিলিত সুর শোনা যায়।
অপরদিকে, সারনাথের বুদ্ধমূর্তি যেন পাথরের মধ্যে ধ্যানের ভাষা খোদাই করে। গুপ্ত যুগের বুদ্ধমূর্তিগুলোতে আমরা যে শান্ত, সমাহিত ও আধ্যাত্মিক ভঙ্গি দেখি, তা ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে। ভারী অলংকার বা অতিরঞ্জিত ভঙ্গির পরিবর্তে এখানে রয়েছে সংযম, সরলতা ও অভ্যন্তরীণ দীপ্তি। বুদ্ধের অর্ধনিমীলিত চোখ যেন বহির্জগতের কোলাহল অতিক্রম করে অন্তর্জগতের দিকে আহ্বান জানায়। এই মূর্তিগুলো কেবল উপাসনার বস্তু নয়; এগুলো দর্শনের প্রতিমূর্তি—যেখানে মুক্তি, করুণা ও প্রজ্ঞা একত্রে রূপ পেয়েছে।
গুপ্ত যুগে মন্দির স্থাপত্যে দেবগড়, ভীতরগাঁও ও নালন্দার নিদর্শনগুলো ভারতীয় শিল্পের এক নতুন ভাষা নির্মাণ করে। এই মন্দিরগুলোতে আমরা প্রথমবারের মতো কাঠামোগত মন্দির স্থাপত্যের সুস্পষ্ট রূপ দেখি। শিখর, গর্ভগৃহ ও মণ্ডপের বিন্যাস ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ করে। এই স্থাপত্যশৈলীতে সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকী অর্থও গভীরভাবে যুক্ত। মন্দির শুধু ইট-পাথরের নির্মাণ নয়; এটি ছিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ, যেখানে মানুষ ক্ষুদ্র সত্তা হিসেবে দাঁড়িয়ে অসীমের সন্ধান করে।
গুপ্ত যুগে সংস্কৃত সাহিত্যও অভূতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করে। কালিদাসের কাব্য ও নাটকে প্রকৃতি, প্রেম ও মানব-মনস্তত্ত্বের যে সূক্ষ্ম চিত্রণ দেখা যায়, তা এই যুগের নন্দনচেতনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। “অভিজ্ঞানশকুন্তলম” বা “মেঘদূত”-এ সৌন্দর্য কেবল দৃশ্যমান নয়; তা অনুভূতির স্তরে প্রসারিত। এ যুগে ভাষা ছিল কেবল ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়; ভাষা নিজেই হয়ে উঠেছিল শিল্প।
অতএব গুপ্ত যুগকে “স্বর্ণযুগ” বলা হয় শুধু তার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য নয়, বরং এই কারণে যে এই যুগে সৌন্দর্য ছিল জীবনদর্শনের কেন্দ্রে। শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে এবং বিশ্বকে নতুনভাবে বুঝতে শিখেছিল। গুপ্ত যুগ আমাদের শেখায়—সভ্যতার প্রকৃত মহিমা তার বাহ্যিক জৌলুসে নয়, বরং তার অন্তর্লীন মানবিক ও নান্দনিক চেতনায়। সাহিত্য মূলতঃ শব্দের মধ্যে দর্শন। গুপ্ত যুগের সাহিত্য ভারতীয় মননের এক শীর্ষবিন্দু। কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম’, ‘মেঘদূত’, ‘কুমারসম্ভব’ সবই কেবল কাব্য নয়; এগুলি দর্শনের ভাষা, ভারতীয় জীবনের ভাষ্য। কালিদাস প্রকৃতিকে দেখেন কেবল দৃশ্য হিসেবে নয়; প্রকৃতি তাঁর কাছে আত্মার প্রতিচ্ছবি। পুরাণ সাহিত্য এই সময়ে ইতিহাস ও কল্পনার এক সেতুবন্ধন রচনা করে। বিষ্ণু, শিব, দেবী—এই তিন ধারার মধ্য দিয়ে ভারতীয় ধর্মচিন্তা নতুন রূপ পায়।
ভারতীয় সভ্যতার একটি বড় ভুল ব্যাখ্যা হলো- এটি নাকি কেবল আধ্যাত্মিক, যুক্তিবাদী নয়। গুপ্ত যুগ এই ধারণাকে ভেঙে দেয়। আর্যভট লিখলেন, “পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর ঘোরে।” এরপর ব্রহ্মগুপ্ত শূন্যের ধারণাকে গাণিতিক রূপ দিলেন । এই আবিষ্কারগুলি প্রমাণ করে যে ভারতীয় মনন একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক। শুধুমাত্র দাবি নয় এখন ইটা প্রমাণিত সত্য যে গুপ্ত যুগে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রগতিও উল্লেখযোগ্য। শূন্যের ধারণা, দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বিকাশ, আর্যভট্টের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইত্যাদি প্রমাণ করে যে এই যুগে যুক্তিবোধ ও কল্পনাশক্তি পরস্পরের বিরোধী ছিল না, বরং পরস্পরকে পরিপূরক করেছিল। এই সমন্বয়ই গুপ্ত যুগের প্রকৃত শক্তি।
মৌর্য–গুপ্ত যুগে বৌদ্ধ বিহার, জৈন মঠ ও হিন্দু মন্দির একসঙ্গে বিকশিত হয়। এই সহাবস্থান কোনো আপস নয়; এটি ভারতীয় সভ্যতার মৌল চরিত্র। বৌদ্ধ দর্শন প্রশ্ন করে, বৈদিক দর্শন উত্তর দেয়, জৈন দর্শন সংযমের পথ দেখায়। এই তিন ধারার মধ্যেই নিহিত আছে ভারতীয় চিন্তার পূর্ণতা। আবার চার্বাক দর্শন আবার সমস্ত আধ্যাত্মিক ধারণাকে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে, “যাবৎ জীবেত সুখং জীবেত, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত।”
এই বস্তুবাদী জীবন দর্শন ভারতীয় চিন্তার বহুত্বকে আরও গভীর করে। অন্যদিকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মৌর্য–গুপ্ত যুগ ভারতীয় সমাজের এক দীর্ঘ রূপান্তরের সময়। বর্ণব্যবস্থা, গ্রামসমাজ, নগরায়ণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সবকিছুই নতুন রূপ পায়। সংস্কৃতায়ন ও প্রতিসংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ভারতীয় সমাজকে গতিশীল রাখে। নিম্নবর্গীয় ও প্রান্তিক মানুষ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুকরণ ও অনুসরণ করে সামাজিক মর্যাদা অর্জন করে, আবার শ্রমণ আন্দোলন এই কাঠামোকেও বারবার প্রশ্ন করে। এই দ্বৈত প্রক্রিয়াই ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ।
আজকের ভারত যখন ধর্মীয় মেরুকরণ, পরিচয় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক সংকটে আক্রান্ত, তখন মৌর্য–গুপ্ত যুগ আমাদের সামনে এক বিকল্প মডেল হাজির করে। এই যুগ দেখায় যে সভ্যতা শক্তিশালী হয় বহুত্বে, দুর্বল হয় একমাত্রিকতায়।
মৌর্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সাধারণত উত্তর ভারতের রাজনৈতিক উত্থান, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিন্দুসার ও অশোকের শাসনকেন্দ্রিক কাহিনিই প্রাধান্য পায়। কিন্তু এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের ছায়ায় দক্ষিণ ভারতও নীরবে এক স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে এগোচ্ছিল। মৌর্যযুগে দক্ষিণ ভারত সরাসরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, তার সঙ্গে গভীর রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ গড়ে উঠেছিল। এই সংযোগই পরবর্তী দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতার ভিত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমা মূলত দাক্ষিণাত্যের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের শিলালিপিতে চোল, চের, পাণ্ড্য ও সত্যপুত্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে যে এই রাজ্যগুলি মৌর্যদের সমসাময়িক ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিদ্যমান ছিল।
দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যের অধীনস্থ না হয়েও মৌর্য প্রশাসনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক- দক্ষিণ ভারত তখনও স্বাধীন, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। বরং এক বৃহত্তর ভারতীয় রাজনৈতিক পরিসরের অংশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করছিল। মৌর্যযুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে স্থল ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ ভারত ছিল মসলা, মূল্যবান পাথর, মুক্তা, হাতির দাঁত ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই পণ্যগুলি উত্তর ভারতের বাজারে পৌঁছাত, আবার উত্তর ভারত থেকে ধাতব দ্রব্য, অস্ত্র ও মুদ্রা দক্ষিণে যেত। ফলে দক্ষিণ ভারতের বন্দরনগরীগুলি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাণিজ্যের এই প্রসার কেবল অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও ঘটায়- ধারণা, বিশ্বাস ও শিল্পরীতির বিনিময় সম্ভব হয়।
মৌর্যযুগে দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলির একটি হলো বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিস্তার। অশোকের ধর্মপ্রচার নীতির ফলে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দক্ষিণ ভারতে গমন করেন। পাহাড়ের গুহা, শিলাশ্রয় ও অরণ্যাঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন আশ্রম গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে দক্ষিণ ভারতের মানুষ অহিংসা, করুণা ও সংযমের দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই ধর্মীয় প্রভাব দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতিতে এক মানবিক ও নৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলে, যা পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে সাহিত্য ও শিল্পে গভীর ছাপ ফেলে। মৌর্যযুগে দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষার ভিত্তি আরও দৃঢ় হতে থাকে। যদিও সংগঠিত তামিল সাহিত্য পরবর্তীকালে সঙ্গম যুগে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে, তবু এই সময়েই মৌখিক কাব্য, গান ও বীরগাথার চর্চা শুরু হয়েছিল। এই সাহিত্যধারায় প্রকৃতি, প্রেম, বীরত্ব ও সামাজিক মর্যাদার বিষয়গুলি গুরুত্ব পায় যা উত্তর ভারতের ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের তুলনায় এক ভিন্ন স্বর সৃষ্টি করে।
মৌর্যযুগে দক্ষিণ ভারতে বৃহৎ পাথরের স্তম্ভ বা রাজকীয় স্থাপত্যের ব্যাপক নিদর্শন না মিললেও, গুহাকেন্দ্রিক স্থাপত্য ও শিলাশ্রয় শিল্পের সূচনা হয়। বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য নির্মিত গুহাগুলিতে সরল নকশা, ধ্যানকক্ষ ও ধর্মীয় চিহ্ন দেখা যায়। এই ধারা পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতের বিশাল মন্দির স্থাপত্যের ভিত্তি তৈরি করে।
দক্ষিণ ভারতের সমাজ তখন মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। কৃষক, জেলে, পশুপালক ও কারিগরদের নিয়ে গঠিত এই সমাজে বর্ণব্যবস্থার কঠোরতা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। গোষ্ঠীগত সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি। নারীরাও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন—যার প্রতিফলন পরবর্তী তামিল সাহিত্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মৌর্যযুগে দক্ষিণ ভারত একদিকে নিজস্ব সংস্কৃতি লালন করছিল, অন্যদিকে উত্তর ভারতের ধর্মীয় ও দার্শনিক ধারা গ্রহণ করছিল। এই দ্বিমুখী প্রবাহ ভারতীয় সভ্যতাকে আরও সমৃদ্ধ করে। দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি তাই এই সময়েই একটি স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলতে শুরু করে যা পরবর্তীকালে চোল, চের ও পাণ্ড্যদের মহিমায় পূর্ণ বিকাশ লাভ করে।
মৌর্যযুগে দক্ষিণ ভারত কোনো নিঃশব্দ প্রান্তভূমি ছিল না; বরং এটি ছিল এক সজীব চলমান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, যেখানে স্বাধীন রাজনীতি, সক্রিয় বাণিজ্য ও নৈতিক-দার্শনিক চিন্তার বিকাশ একসঙ্গে ঘটছিল। এই যুগে দক্ষিণ ভারত যে ভিত্তি নির্মাণ করেছিল, তার ওপর দাঁড়িয়েই পরবর্তী কালে দক্ষিণ ভারতের গৌরবময় সভ্যতা গড়ে ওঠে। মৌর্যযুগ তাই দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এক নীরব কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এক কথায় বলাযায় , মৌর্য–গুপ্ত যুগ কোনো অতীত অধ্যায় নয়। এটি ভারতীয় আত্মার এক দীর্ঘ সাধনা। এখানে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে নৈতিকতায় উত্তীর্ণ হয়, ধর্ম সংকীর্ণতা থেকে বহুত্বে বিস্তৃত হয়, শিল্প সৌন্দর্য থেকে দর্শনে পৌঁছায়, আর মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে বিশ্ব-মানব হিসেবে। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস তাই কেবল রাজাদের ইতিহাস নয়; এটি মানুষের আত্মার ইতিহাস। আর সেই ইতিহাস আজও বহমান ধারা ।